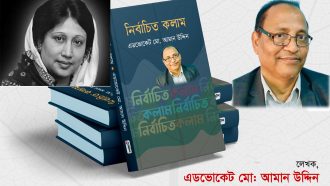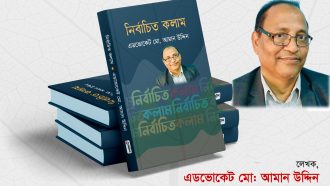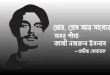রাজনীতির অনিশ্চয়তা এখন কতটা গভীর
১৯ ফেব্রু ২০২৫, ০১:১০ অপরাহ্ণ

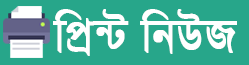
এ কে এম জাকারিয়া:
অন্তর্বর্তী সরকার ছয় মাস পার করেছে, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে—এমন একটি ধারণাও তারা দিয়েছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অবশ্য দ্য ন্যাশনাল সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সবচেয়ে সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে সংস্কারের প্রয়োজনে আরও তিন মাস লাগতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। মূল ছয়টি সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে তাদের প্রতিবেদন দিয়ে দিয়েছে।
সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। দেশে একটা নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরি এবং এই পরিস্থিতি স্বস্তি দেওয়ার কথা। কিন্তু দেশের রাজনীতিতে তো টের পাওয়া যাচ্ছে অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি।
কেন এই অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি? সাধারণভাবে উত্তরটি হচ্ছে, সবাই এখন নিজ নিজ চাওয়া-পাওয়া নিয়ে এগোতে চাচ্ছে এবং গণ-অভ্যুত্থানের শক্তিগুলোর এই চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে। কখন নির্বাচন, কোন পর্যন্ত সংস্কার বা সরকারের মেয়াদ—এসব নিয়ে আসলে পক্ষগুলোর মধ্যে বড় মতপার্থক্য রয়েছে।
দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল ভূমিকা পালনকারী পক্ষগুলোকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি এভাবে—গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রসমাজ (অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ছাত্রসংগঠনগুলো বাদে), সরকার, বিএনপি ও সহযোগী কিছু রাজনৈতিক দল, জামায়াতে ইসলামী ও কিছু ইসলামি রাজনৈতিক দল এবং সেনাবাহিনী।
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের ভাষণে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর অথবা ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছিলেন। এর আগে তিনি এমন ধারণা দিয়েছিলেন, যাতে মনে হয়েছিল যে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ তিন থেকে সাড়ে তিন বছর হতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যেও মেয়াদ নিয়ে মতভিন্নতার কথা শোনা যায়।
সেনাপ্রধান বলেছিলেন, ১৮ মাসের মধ্যেই নির্বাচন হওয়া উচিত। এ বছর ডিসেম্বরে নির্বাচন হলে তাঁর চাওয়ার সঙ্গে মিলে যাবে। বিএনপি যত দ্রুত সম্ভব নির্বাচন চায়। তাদের পক্ষ থেকে এ বছর জুলাই-আগস্টের মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের দাবিও তোলা হয়েছে। তাদের সহযোগী ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোও তা-ই চায়। ছাত্ররা দ্রুত নির্বাচনের পক্ষে নন, তাঁরা প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নির্বাচন করার পক্ষে। জামায়াতে ইসলামী বা অন্য ইসলামি দলগুলোর দ্রুত নির্বাচন নিয়ে কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। তারা সরকারকে সময় দিতে চায়।
২.
গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের দল গঠনের উদ্যোগ রাজনীতিতে নতুন মাত্রা দিয়েছে। দলের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। গণ-অভ্যুত্থান বা এ ধরনের যেকোনো আন্দোলনে দেশের ছাত্রসমাজ সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কী অবস্থান নিয়েছিল, তা আমরা জানি। কিন্তু ২৪–এর গণ-অভ্যুত্থানের চরিত্র আলাদা।
নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্রসংগঠনগুলো নিজেদের মূল রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থানের প্রতিই অনুগত থেকেছে। এরপরের রাজনৈতিক ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরা মিলে ‘তিন জোটের রূপরেখা’ তৈরি করলেও তারা জনগণকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।
চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্ররা দেশের কোনো প্রচলিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করেন না। এসব ছাত্রের নেতৃত্বে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও তাদের সহযোগী সংগঠনগুলো (ছাত্রসংগঠনসহ) গণ-অভ্যুত্থানে শামিল হয়েছে। কোনো সন্দেহ নেই যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় না থাকায় দেশের সব স্তরের জনগণও কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে থাকা রাজনৈতিক শক্তি ও জনগণ—এই দুই পক্ষ ছাত্রদের নেতৃত্বে মাঠে নামায় হাসিনার মতো নিপীড়ক শাসককে সরানো গেছে।
দেশের বর্তমান রাজনীতিতে বেশ কিছু পক্ষের ভূমিকা থাকলেও গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রসমাজ ও সবচেয়ে বড় সহায়ক রাজনৈতিক শক্তি বিএনপিকে কেন্দ্র করেই বাকি পক্ষগুলোর হিসাব–নিকাশ চলবে। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বিএনপির যেকোনো বিরোধ, ভুল–বোঝাবুঝি বা সন্দেহ-অবিশ্বাস তাই দেশের রাজনীতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। দুই পক্ষের মধ্যে মৌলিক ও ন্যূনতম কিছু ইস্যুতে মতৈক্যে আসার কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
এবারের গণ-অভ্যুত্থানের পর দেশের রাজনীতিতে ছাত্ররা শুরু থেকেই একটি শক্তি বা অংশীদার হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে সচেষ্ট আছে। সব রাজনৈতিক দলের সম্মতিতে যে অন্তর্বর্তী সরকার হয়েছে, সেখানে কোনো দলের প্রতিনিধি না থাকলেও ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব আছে। এটা স্পষ্ট যে সেই ধারাবাহিকতায়ই ছাত্রদের নেতৃত্বে দল গড়ে উঠছে।
ছাত্ররা শুরু থেকেই বলে আসছে যে গণ-অভ্যুত্থানের চাওয়া-পাওয়াকে তাঁরা ব্যর্থ হতে দিতে চান না। সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে দেশে আবার আগের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ফিরে আসবে, সেই ভয় ছাত্রদের রয়েছে। নব্বইয়ের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিলে ছাত্রদের এই আশঙ্কা ফেলে দেওয়া যায় না। কোনো রাজনৈতিক দল তিন জোটের রূপরেখা বাস্তবায়নের পথ ধরেনি। ছাত্রদের ১০ দফার কথাও কেউ মনে রাখেনি। ছাত্ররা তাই বিএনপির মতো দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে সরব নন। তাঁরা চান এমন মাত্রার সংস্কার, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর হাসিনার মতো স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে।
অন্যদিকে অন্তর্বর্তী সরকারে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব থাকায় তা এক অর্থে ছাত্রদের সরকারও। তাদের দল গঠনের উদ্যোগকে তাই ‘কিংস পার্টি’ হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে। সরকারের একজন উপদেষ্টা পদত্যাগ করে নতুন দলের নেতৃত্ব নেবেন, তবে আরও দুজন ছাত্র প্রতিনিধি কিন্তু সরকারে থেকে যাচ্ছেন। ফলে সরকার ও ছাত্রদের নতুন দলের মধ্যে একটি যোগসূত্র থাকছেই। এসব কারণে নতুন দল গঠনে সরকার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সহযোগিতা বা প্রভাব এবং অর্থের উৎস নিয়ে একধরনের অস্বচ্ছতা ও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।
ছাত্ররা চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে— এই সত্য নিয়ে কারও মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এটাও মনে রাখা জরুরি যে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গত ১৬ বছর ধরে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন জারি রেখেছিল। এসব রাজনৈতিক দলের অনেক নেতা-কর্মী প্রাণ দিয়েছেন, জেল-জুলুম ও গুমসহ নানা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। কোনো কিছুর একক কৃতিত্ব দাবি করার প্রবণতা আখেরে ভালো ফল দেয় না। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আওয়ামী লীগ এই কাজ করেছে, এর ফল এখন তারা ভোগ করছে।
৩.
অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রদের সঙ্গে নানা ইস্যুতে বিএনপির বিরোধ বেশ আগেই শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রপতির অপসারণ, জুলাই অভ্যুত্থানের ঘোষণা ইত্যাদি প্রশ্নে দুই পক্ষের অবস্থান ছিল ভিন্ন। বিএনপির কারণে ছাত্রদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আবার ছাত্রদের নানা তৎপরতা নিয়েও বিএনপির মধ্যে অস্বস্তি রয়েছে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর ভেঙে ফেলাকে বিএনপি ভালোভাবে নেয়নি বলেই জানা যায়।
ছাত্র-তরুণদের দল গঠনের উদ্যোগকে বিএনপি স্বাগত জানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছাত্রদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা বা দল গঠন নিয়ে তাদের মধ্যে একধরনের অস্বস্তি, সন্দেহ ও অবিশ্বাস রয়েছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ভাষায়, রাজনৈতিক দল গঠন করতে গিয়ে কেউ যদি রাষ্ট্রীয় কিংবা প্রশাসনিক সহায়তা নেন, সেটি জনগণকে হতাশ করবে। তা ছাড়া মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি যে লিখিত বক্তব্য দিয়েছে, সেখানেও একই উদ্বেগ তুলে ধরা হয়েছে।
গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের পতনের পর বিএনপিই দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক শক্তি। আগের হিসাব–নিকাশে আওয়ামী লীগের বিদায় মানেই বিএনপির ফিরে আসা। কিন্তু এখন দিন যত যাচ্ছে, তাদের মনে সন্দেহ বাড়ছে। বিএনপি মনে করছে, তারা যাতে ক্ষমতায় আসতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে চাইছে কোনো কোনো পক্ষ। তারেক রহমান সেদিনও বলেছেন, ষড়যন্ত্র চলছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কিছু কি সত্যিই ঘটছে? এর জবাবে বলা যায়, রাজনীতির অন্দরমহলে কী ঘটে বা ঘটছে, তা আঁচ করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই বিএনপির মতো দলের আছে।
বিএনপি মনে করে, দল গঠনের সুবিধার জন্যই ছাত্ররা নির্বাচন পেছানোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। অন্যদিকে বিএনপি সম্ভবত এটা জানে যে নির্বাচনের যত বিলম্ব হবে, দলটি তত বিপদে পড়বে। আওয়ামী লীগের পতনের পর বিএনপি ক্ষমতায় এসে গেছে মনে করে দলটির স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা তৎপর হয়েছেন। দখল, নিয়ন্ত্রণ ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছেন অনেকে। দেশজুড়েই এসব ঘটনা ঘটছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা বা বহিষ্কারের মতো পদক্ষেপও তাঁদের থামাতে পারছে না। এসব ঘটনা নিশ্চিতভাবেই বিএনপির জনপ্রিয়তা ও ভোট কমাবে।
গণ-অভ্যুত্থান নতুন রাজনীতির আশা জাগিয়েছে। দেশের মানুষ আর পুরোনো রাজনীতিতে ফিরতে চায় না। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব যদি তা বুঝেও থাকেন, স্থানীয় পর্যায়ে বা সাধারণ কর্মী-সমর্থকেরা যে তা আমলে নিচ্ছেন না তা তাদের কর্মকাণ্ডেই স্পষ্ট। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, দ্রুত নির্বাচন এবং ক্ষমতায় এসে বিএনপি কি তার দলের নিয়ন্ত্রণহীন এসব নেতা-কর্মীদের সামলাতে পারবে? নাকি আগের পুরোনো ধারায় আওয়ামী লীগের বদলে বিএনপি— এই রাজনীতিই ফিরে আসবে? সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে এবং পুরোনো রাজনীতি ফিরে আসা নিয়ে তাদের মধ্যে ভয় আছে।
৪.
দেশের বর্তমান রাজনীতিতে বেশ কিছু পক্ষের ভূমিকা থাকলেও গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রসমাজ ও সবচেয়ে বড় সহায়ক রাজনৈতিক শক্তি বিএনপিকে কেন্দ্র করেই বাকি পক্ষগুলোর হিসাব-নিকাশ চলবে। ছাত্রনেতাদের সঙ্গে বিএনপির যেকোনো বিরোধ, ভুল-বোঝাবুঝি বা সন্দেহ-অবিশ্বাস তাই দেশের রাজনীতিকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিতে পারে। তার কিছু লক্ষণ এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দুই পক্ষের মধ্যে মৌলিক ও ন্যূনতম কিছু ইস্যুতে মতৈক্যে আসার কোনো বিকল্প নেই। তা না হলে গণ-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
● এ কে এম জাকারিয়া প্রথম আলোর উপসম্পাদক
akmzakaria@gmail.com
এই সংবাদটি পড়া হয়েছে : 1.1K বার